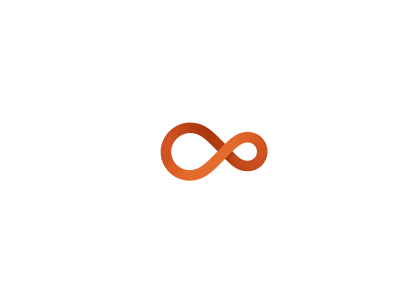সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্যাম বেনগাল একটা কথা বলতেন, 'তিনি হচ্ছেন প্রথম একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ,
যিনি ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি তৈরি করেছেন।'
তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয়, এই ভারতীয় পদ্ধতি ব্যাপারটি কী? চলচ্চিত্র মাধ্যমটি এসেছে পাশ্চাত্য থেকে। সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন বা
শিল্প বলুন---এগুলির প্রত্যেকটির এক একটি পৃথক মাধ্যম আছে। যার দ্বারা সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁদের নিজেদের বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন। চলচ্চিত্র বা সিনেমা এই নতুন মাধ্যমটি অনেকগুলি শিল্পের সমষ্টি হলেও এর মূল ভাষা চলমান চিত্রের মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরা। সত্যজিৎ নিজেই জানিয়েছিলেন, ‘লেখকের হাতে যেমন কথা, চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমননি ছবি (image) ও শব্দ(sound)।
এই দুইয়ে মিলে যে ভাষা, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি মুনশিয়ানার অভাব হয়, তার ব্যাকরণ যদি রচয়িতার আয়ত্ত না থাকে এবং সব মিলিয়ে ছবির বক্তব্যে যদি জোর না থাকে, তা হলে ভালো ছবি হবে কী করে?'
সত্যজিতের বিষয়টির প্রতি সম্যক ধারণা ছিল বলে প্রথম ছবিতেই তিনি সেটা দেখিয়ে বিদগ্ধ মহলে যথেষ্ট নজর কাড়তে সক্ষম হন। সিনেমার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর কলেজ জীবন থেকেই। বিদেশি ছবি দেখে নানান জিনিস তিনি আগ্রহ ভরে শিখেছিলেন। আইজেনস্টাইনের ছবি দেখে শিখেছিলেন সিনেমার ব্যাকরণ, হলিউডের ছবি দেখে জেনেছেন কী করে সিনেমায় গল্প বলতে হয়, ইতালির নিওরিয়ালিজমের কাছ থেকে শিখেছেন কী করে চলচ্চিত্রে সমাজের বাস্তব চেহারাটা তুলে ধরতে হয়। এই সব কিছু শিখেই তিনি দেখালেন বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও বাঁচার অদম্য ইচ্ছেটাকে সুস্থ রুচির মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। সত্যজিতের প্রথম ছবিতেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তিনি সিনেমার নিজস্ব ভাষাতে ভারতীয় শিল্পের ভাষাকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় শিল্পী যেমন সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে নিতে চান, তিনিও প্রকৃতির সঙ্গে চরিত্রের মনের কথা, আনন্দের অভিব্যক্তি, দুঃখের প্রকাশকে মিলিয়ে দিলেন। নন্দলাল বসুর শিক্ষাকে, শিল্পের স্বভাব, পরম্পরা আর স্বকীয়তা প্রয়োগ করে এক সর্বাঙ্গসুন্দর আর্টের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। অতিকথনে না গিয়েও পল্লীজীবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করলেন। পাশাপাশি বাংলার গ্রামের মানুষের ব্যবহারের ক্ষুদ্রতা, তার পাশে সহানুভূতি, রুক্ষ কর্কশ ব্যবহারের পাশে স্নেহময় মাতৃত্ব, বাঁচার ইচ্ছের পাশে মৃত্যু সব কিছুকে ছন্দময় ভাবে দেখালেন। ভারতীয় দর্শন এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে আত্মস্থ করে তিনি মনন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্পের ভাষায় খাঁটি ভারতীয় হয়েও এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।
চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ রায় তাঁর চল্লিশ বছরের জীবনে মোট ২৮টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্র, পাঁচটি তথ্যচিত্র এবং টেলিভিশনের জন্যে তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা তৈরি করেছেন। এছাড়া তিনি অন্য পরিচালকের জন্যে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন , এমনকি তথ্যচিত্রের জন্যেও চিত্রনাট্য বা সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, তাঁর কাজের সঙ্গে আগের ভারতীয় ছবির কাজের তেমন কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সত্যজিৎ তাঁর ছবিকে সবসময় জীবনানুগ করেই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ছবির বৈশিষ্ট্য ছিল নিত্যনূতন বিষয়।
সত্যজিৎ প্রথমে তাঁর ছবির কাহিনির জন্যে বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় উপন্যাস বা গল্প নির্বাচন করেছিলেন। পরের দিকে সমকালীন লেখকদের কাহিনি, কখনও বা নিজেই রচনা করেছেন তাঁর ছবির চিত্রনাট্য ও কাহিনি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর, প্রেমচন্দ এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে ইবসেনের নাটক এবং নিজের কাহিনি ভিত্তিক চলচ্চিত্র সৃষ্টি করে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতকে ঋদ্ধ করে গিয়েছেন।
'অপুর সংসার' ছবিতে একটি দৃশ্যে অপু তার বন্ধু গুলুকে একটি আশ্চর্য উপন্যাসের কথা শুনিয়েছে। অপু বলছে, 'একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে, দরিদ্র, কিন্তু sensitive, বাপ পুরুত। মারা গেল। ছেলেটি শহরে এল, সে পুরুতগিরি করবে না, পড়বে। Ambitious। পরে শিক্ষার ভেতর দিয়ে , struggle-এর ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কুসংস্কার, গোঁড়ামি সমস্ত কেটে যাচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে ছাড়া সে কোনো কিছু মানতে চাইছে না। কিন্তু তার কল্পনাশক্তি আছে। তার অনুভূতি আছে। ছোটখাটো জিনিস তাকে move করছে, তাকে আনন্দ দিচ্ছে। হয়ত তার ভিতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে, সম্ভাবনা আছে, কিন্তু করছে না। কিন্তু সেইটাই শেষ কথা নয়--সেটা ট্রাজেডিও নয়-- সে মহৎ কিছু করছে না। তার দারিদ্র্য যাচ্ছে না। তার অভাব মিটছে না, তা সত্ত্বেও সে জীবনবিমুখ হচ্ছে না, সে পালাচ্ছে না। Escape করছে না। সে বাঁচতে চাইছে। সে বলছে, বাঁচার মধ্যেই সার্থকতা, তার মধ্যেই আনন্দ।'
এই কাহিনিটাই আসলে অপু চিত্রত্রয়ীর কাঠামো। প্রথম ছবিতেই সত্যজিৎ দেখালেন সংক্ষিপ্ত অথচ স্বাভাবিক সংলাপ, পরিবেশের শব্দ আর সঙ্গীত দিয়ে কীভাবে চলচ্চিত্রকে গভীর ও মর্মস্পর্শী করে তোলা যায়। তিনি দেখালেন বাঙালির ঘরের কথাকে কীভাবে বিশ্বজনীন করে তোলা যায়। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' --- প্রথম এই দুটি ছবিতেই তিনি নিজেকে ভারতীয় ছবির জগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ' অপরাজিত ' এবং 'অপুর সংসার' তৈরির মধ্যেই তিনি তৈরি করেছেন দুটি ভিন্ন গোত্রের ছবি 'পরশ পাথর' ও 'জলসাঘর'।
অর্থনৈতিক আঘাতে জর্জরিত দরিদ্র এক কেরানির স্বপ্ন দেখার ছবি 'পরশ পাথর'। বিত্তহীন মধ্যবিত্তের জীবন বেদনা, ব্যর্থতা আর বঞ্চনার ছবি। আবার হাসির মোড়কে দুঃখের চলচ্চিত্র বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না।
পরের ছবি 'জলসাঘর'- এর বিষয় ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গীতপ্রিয় এক মানুষের কথা। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের আচরণ, কথাবার্তায় দম্ভ ও আভিজাত্য ফুটে উঠলেও তাঁর প্রাসাদে বা অর্থনৈতিক অবস্থায় পড়ন্ত অবস্থার ছাপ স্পষ্ট। উল্টোদিকে সেসব ছাপিয়ে নব্য বিত্তবানের শিল্পযন্ত্রের শব্দ বা মোটর গাড়ির ধুলোতে ঢেকে যাওয়া জমিদারের হাতি --- এমনি সব দৃশ্যের সমন্বয়ে, অভিনয়ে, মন্তাজে সত্যজিতের এক অনবদ্য ছবি 'জলসাঘর'। 'দেবী' ছবিটিকে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদী চলচ্চিত্র' হিসেবে ধরাই যায়। একই সঙ্গে গত শতাব্দীর বাঙালি মানসিকতায় বিচিত্র জটিল ট্র্যাজেডি হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। ধর্মীয় কুসংস্কারের মানসিকতার অমানবিক এবং অবৈজ্ঞানিক সামাজিক চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন 'দেবী' ছবিটিতে।
রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষে সত্যজিৎ তিন বয়সের তিন কন্যার তিনটি কাহিনিতে তাদের অনুভূতির তিনটি ভিন্ন স্তর অসাধারণ মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে
তুলেছিলেন। অসমান বয়সের দুটি চরিত্রের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-স্নেহের সম্পর্কের ভাঙন পরে মিলনের ছবি 'সমাপ্তি'। 'মণিহারা'র কাহিনিতে রয়েছে রহস্যময়তা। এই ছবি থেকেই সত্যজিৎ নিজের ছবিতে নিজেই সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন। চরিত্রের মানসিকতা বা ঘটনামুহূর্ত বোঝাবার জন্যে সত্যজিতের সঙ্গীত যে যথাযথ হয়েছিল, তা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।
কলকাতার উচ্চবিত্ত, অভিজাত, কেতাদুরস্ত মধ্যবিত্ত আর সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানসিকতার কয়েকজন মানুষের আত্মিক সঙ্কট, এবং সংঘাত মোচনের আভাস নিয়েই 'কাঞ্চনজঙ্ঘা '। এর আগে তিনি সবকটি কাহিনিচিত্রের মূল ভাবনাটি অন্য লেখকের সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রথম তিনি নিজের কাহিনি নিয়েই ছবি করলেন। পরিবেশ, আউটডোরের ওপর নিচ রাস্তা, চরিত্রদের পোশাক, ক্যামেরার
দৃষ্টিকোণ সব কিছু মিলে একটি খাঁটি চলচ্চিত্রের উদাহরণ ছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। তবে সত্যজিৎ পরে স্বীকার করেছিলেন, বাঙালি দর্শকদের জন্যে ছবিটি সময়ের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিল। 'চারুলতা' ছবির ক্ষেত্রে বলা যায়, এর প্রতিটি দৃশ্য, পাত্র-পাত্রীর অভিব্যক্তি, সংলাপ, দৃশ্য পরম্পরায় এমন নিখুঁত ছবি ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে। ত্রিকোণ সম্পর্কের প্রসঙ্গে বলা যায় 'চারুলতা'র তুলনায় 'ঘরে বাইরে'র পটভূমি বৃহত্তর। তুলনায় খুবই সাধারণ উপাদান নিয়ে , কেবলমাত্র চিত্রনাট্যে ব্যাপ্তি এনে চলচ্চিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তাঁর 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে। এই ছবির পিকনিকে 'মেমরি গেম'-এর দৃশ্যে চরিত্রগত অবস্থান, তাদের সংলাপ, আবেগ-অনুভূতির স্তরভেদে এক অনন্য দৃশ্য রচনা করেছিলেন।
তাঁর কলকাতা ভিত্তিক ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে 'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' ও 'জনঅরণ্য'। জীবিকার সন্ধানে জীবনযুদ্ধ, শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান, সরকার বিরোধী আন্দোলন, অনাচারের মধ্য দিয়ে চাকরি জীবনের উন্নতির সন্ধান সব কিছুই তিনি শ্লেষাত্মক, প্রতিবাদী বিশ্লেষণে নির্মাণ করেছিলেন। শ্লেষ-ব্যঙ্গে সমাজকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। সমাজের উচ্চবিত্ত এবং একইসঙ্গে ফিল্মের নায়কের ভূমিকায় অভিনীত ব্যক্তিত্বের চরিত্র বিশ্লেষণের অসাধারণ ছবি 'নায়ক'। পর্দার নায়কের মনোজগতের এক একটি কুঠুরি খুলে গেছে শিক্ষিত সৎ এক মধ্যবিত্ত নারীর সামনে।সিনেমার মাধ্যমের দিক থেকে বলতে হয় সত্যজিতের 'নায়ক' বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ছবি।
'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে', 'সোনার কেল্লা' কিংবা 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিগুলি ছোটোদের জন্যে হলেও বড়দের উপভোগ করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। যদিও এর প্রত্যেকটি ছবিতেই সমাজের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালককে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে দেখা গেছে। একালের আমি সমাজের নানান দুর্নীতি, ধর্মাচরণের নামে কুসংস্কার ও ব্যবসা, সামাজিক ব্যাধিকে বিষয় করে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তে। 'গণশত্রু' ও 'শাখাপ্রশাখা' ছবি দুটি তার প্রমাণ। সভ্যতার সঙ্কটকে কেন্দ্র করেই তিনি বিষয় নির্বাচন করেছিলেন জীবনের শেষ ছবি 'আগন্তুক'-এর। সত্যজিৎ যেন তাঁর জীবনদর্শন দেখাতে চেয়েছিলেন 'আগন্তুক'-এ পরিব্রাজক - আগন্তুক মনমোহন মিত্রের মধ্যে দিয়ে। মনমোহনের ভূমিকায় উৎপল দত্ত যেন সত্যজিতের মুখপাত্র হয়ে অভিনয় করেছিলেন।
বিশ্বের শাশ্বত কিছু নীতি, মানুষের ধর্ম এবং মানব মূল্যবোধের সামগ্রিক চর্চা নিয়েই তাঁর জীবনের শেষ ছবি।