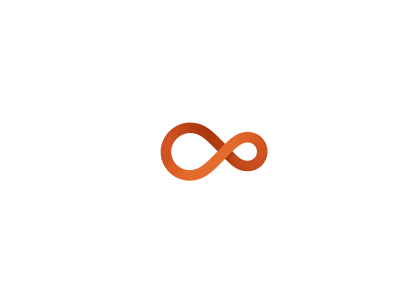সেই কোন ছোটোবেলা থেকে যে এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করে চলেছি, এবং একজন বাংলাভাষী বাঙালি হিসেবে, আজ আর মনেই পড়ে না।
মনে পড়ে, কেনার সামর্থ্য থাকলেও, ছোটোবেলায় আমরা বছরে দু বার নতুন জামা হাতে পেতাম। একটি বা দুটি পেতাম বাঙালির শ্রেষ্ঠ বা বড়ো উৎসব দুর্গাপুজোয়, আরেকটি পেতাম এই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে।
আমাদের যেহেতু ছিল বড়ো বস্ত্র বিপণি, সেকারণে সেদিন দোকানে নতুন খাতা মহরৎ এবং গণেশ পূজা ও ধুমধাম করে হালখাতা বলুন বা মিষ্টিমুখ হত। উৎসব যেহেতু, ফলে ঘরে সেদিনের খাওয়া দাওয়া ছিল আর-পাঁচদিনের চাইতে আলাদা। এবং, যেহেতু আমাদের বস্ত্র ব্যবসা ছিল, সেহেতু আমরা আমাদের দোকানে খুচরা পোশাক বিক্রির জন্য বড়োবাজারের পাইকারী মহাজনদের উপরে নির্ভরশীল ছিলাম। এই পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কেনা বস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে নিজ নিজ দোকান বা বিপণিতে যাঁরা ব্যবসা করতেন তাঁদের মধ্যে যেমন বাঙালি ছিলেন (এঁদের মধ্যে অধিকাংশই আবার ছিলেন পূর্ববঙ্গীয়), পাশাপাশি বহু অবাঙালিও ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ শহর কলকাতায় বাস করে নিজ নিজ ব্যবসার দেখাশোনা করতেন। এবং মহাজনদের ক্ষেত্রেও তাইই।
প্রথমে তুলে ধরি ৭০-৮০-৯০-এর দশকের পয়লা বৈশাখের চিত্র। বাঙালির দোকান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বাংলা বছরের প্রথম দিনটি যে গুরুত্ব সহকারে পালিত হবে, সেটাই ছিল স্বাভাবিক। সারা বছর যেসব বাঁধা খরিদ্দার বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা করতেন, সেসবের দাম ক্রেতারা কেনার সময়ে কিছু টাকা ক্যাশ দিতেন, এবং কিছু বাকি রাখতেন। আবার খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বড়োবাজারের পাইকারী মহাজনদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চলত। অতএব, দিনটি ছিল সন্ধ্যাবেলায় ক্রেতাদের দোকানে এসে আগের পড়ে থাকা পুরাতন ধার শোধ করে, নতুন করে আবার আগামী এক বছরের জন্য লেনদেনের প্রস্তুতি নেবার দিন। যে ক্যাশ বা নগদ টাকা ক্রেতা জমা করতেন, তা সেই বছরের সাতসকালে কালীঘাট মন্দির থেকে পুজো করিয়ে আনা গণেশ মূর্তির সঙ্গে নতুন লাল শালুর মলাটের খাতায় সেই ক্রেতার নামে জমা হত। এবং তৎসহ চলত ক্রেতা ও দোকানদারের কুশল বিনিময় ও মিষ্টিমুখ। এবং, বেশ মনে আছে এই পয়লা বৈশাখের আরেকটি মুখ্য অন্যতম আকর্ষণ ছিল, সেই বছরের বাংলা ক্যালেন্ডার। এই বাংলা ক্যালেন্ডার ছাড়া, তখনকার পয়লা বৈশাখের হালখাতার কথা ভাবাই যেত না।
একইভাবে এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটত আবার বড়োবাজারের পাইকারী মহাজনদের বেলাতেও।
সেখানে কিন্তু মহাজন হিসেবে বাঙালি যেমন ছিলেন, তেমনি পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবাঙালি অর্থাৎ গুজরাতি, সিন্ধ্রি, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি প্রমুখ অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীরাও ছিলেন।
দীর্ঘদিন কলকাতায় ব্যবসা করার সুবাদে এঁদের অধিকাংশই বলতে গেলে বেড়েই উঠেছিলেন বাঙালি সংস্কৃতির ছোঁয়ায়। এঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভালো বাংলা বলতে পারতেন। অতএব, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে তাঁরাও সেই দিনটিকে বিশেষভাবে উদযাপন করতেন। পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের নিজস্ব হালখাতা এবং গণেশপূজাও দিওয়ালির দিন আলাদাভাবে পালন করতেন।
 আবার ছোটোবেলায় বাবার হাত ধরে যখন খুব ভোরবেলায় নতুন বেতের লাল শালু পাতা ঝুড়িতে করে ছোট্ট গণেশ মূর্তি, নূতন লাল কাপড়ে মোড়া খাতা হাতে গিয়েছি কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে, তখন দেখেছি, বাঙালিদের তুলনায় কম হলেও, বেশ কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ীও আমাদের সঙ্গেই একই লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন বাংলা বছরের নতুন খাতা পুজো দেওয়ার জন্য। তবে, যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি আমাদের পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সবাইই বাঙালি, সেহেতু, স্বীকার করে নিতেই হবে যে, সেই বিশেষ দিনটি অবাঙালীদের পরিবারগুলি ঠিক কীভাবে উদযাপন করতেন সেটা সেভাবে দেখে ওঠা আর হয়ে ওঠেনি।
আবার ছোটোবেলায় বাবার হাত ধরে যখন খুব ভোরবেলায় নতুন বেতের লাল শালু পাতা ঝুড়িতে করে ছোট্ট গণেশ মূর্তি, নূতন লাল কাপড়ে মোড়া খাতা হাতে গিয়েছি কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে, তখন দেখেছি, বাঙালিদের তুলনায় কম হলেও, বেশ কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ীও আমাদের সঙ্গেই একই লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন বাংলা বছরের নতুন খাতা পুজো দেওয়ার জন্য। তবে, যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি আমাদের পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সবাইই বাঙালি, সেহেতু, স্বীকার করে নিতেই হবে যে, সেই বিশেষ দিনটি অবাঙালীদের পরিবারগুলি ঠিক কীভাবে উদযাপন করতেন সেটা সেভাবে দেখে ওঠা আর হয়ে ওঠেনি।
যাই হোক, এরপর মোটামুটি ৯০ (বাংলা সন ১৪০০) -এর দশকের শুরু থেকে বাঙালির জীবনের সামাজিক চিত্রটি একটু একটু করে বদলাতে থাকল। অনেকগুলি কারণ ছিল এই পরিবর্তনের, তার মধ্যে কয়েকটি আমি এখানে তুলে ধরছি।
যেমন, সাবেক বা পুরাতন কলকাতা শহরের মানুষের ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। ফাঁকা জায়গা জমিগুলি সব ভরাট হয়ে সেখানে বহুতল আবাসন বা আধুনিক ফ্ল্যাট গড়ে উঠল।
বহু পুরাতন বাঙালি পরিবার, তাঁদের বাপ ঠাকুরদার আমলের বাসভবন, বেশি দামে বা অর্থের প্রলোভনে, কলকাতা শহরে নতুন আসা অবাঙালিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আরও ভিতরের কোনো শহরতলীতে চলে গেলেন। যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁরাও ক্রমশ নিজেদের কৃষ্টি ও লোক সংস্কৃতি ছেড়ে, অবাঙালি সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের স্থান দখল করল নব্য ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল। পয়লা বৈশাখের স্থান দখল করল অনেকটাই ইংরেজি নববর্ষ অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি। পয়লা বৈশাখের গণেশ পুজো ভুলে, মাতামাতি শুরু হল, মহারাষ্ট্রের গণপতি বাপ্পার পুজো নিয়ে। পয়লা বৈশাখের দিনটির চাইতে অনেক বেশি উন্মাদনা দেখা দিল অবাঙালিদের উৎসব ধনতেরস নিয়ে। বর্তমানে বাঙালির পয়লা বৈশাখ টিমটিম করে টিকে আছে কিছু বস্ত্র বিপণিতে।
বিশেষ করে বড়োবাজার অঞ্চলের দোকানগুলিতে তো পয়লা বৈশাখ হালখাতার দিনে আগের সে জৌলুস আর নেই-ই।
এবং এখানেই আরেকটি যে কথা আলাদা করে বলে নিতেই হয় সেটি হচ্ছে, কলকাতা শহরের যত্রতত্র অলিতে গলিতে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা সোনার দোকানের রমরমা ।
এঁরা মূলত পূর্ববঙ্গের স্বর্ণবণিক ; পয়লা বৈশাখ এসব দোকানে খুবই ধুমধাম করে খরিদ্দার আপ্যায়ন হয়, কিন্তু তার মধ্যে কতটা সেই আগের মতো প্রাণ আছে, সেটি বলতে পারব না।
সবশেষে বলি, কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার কথা। কিশোর বয়সে আমরা বইভক্ত পাঠককুল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম যে, কবে সেই বিশেষ দিনটি আসবে, যেদিন পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আমাদের প্রিয় লেখকদের নতুন নতুন বইয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে। সেদিনটি বইপাড়ার প্রতিটি প্রকাশনা দপ্তরে মিষ্টিমুখ এবং লেখক, কবিরা পাঠকের সামনাসামনি সাক্ষাৎ হতেন, সেই সঙ্গে জমত গল্পগুজব আর দেদার আড্ডা। আজও আছে সেই বইপাড়া, কিন্তু আজ আর পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে কোনো লেখকের নতুন বই প্রকাশ, হয় না বলব না, বরং বলি, কমই হয়।
হালখাতা আজও হয়, পয়লা বৈশাখ সেজেগুজে আসে আজও, কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সেদিনকার টান বা আকর্ষণ।